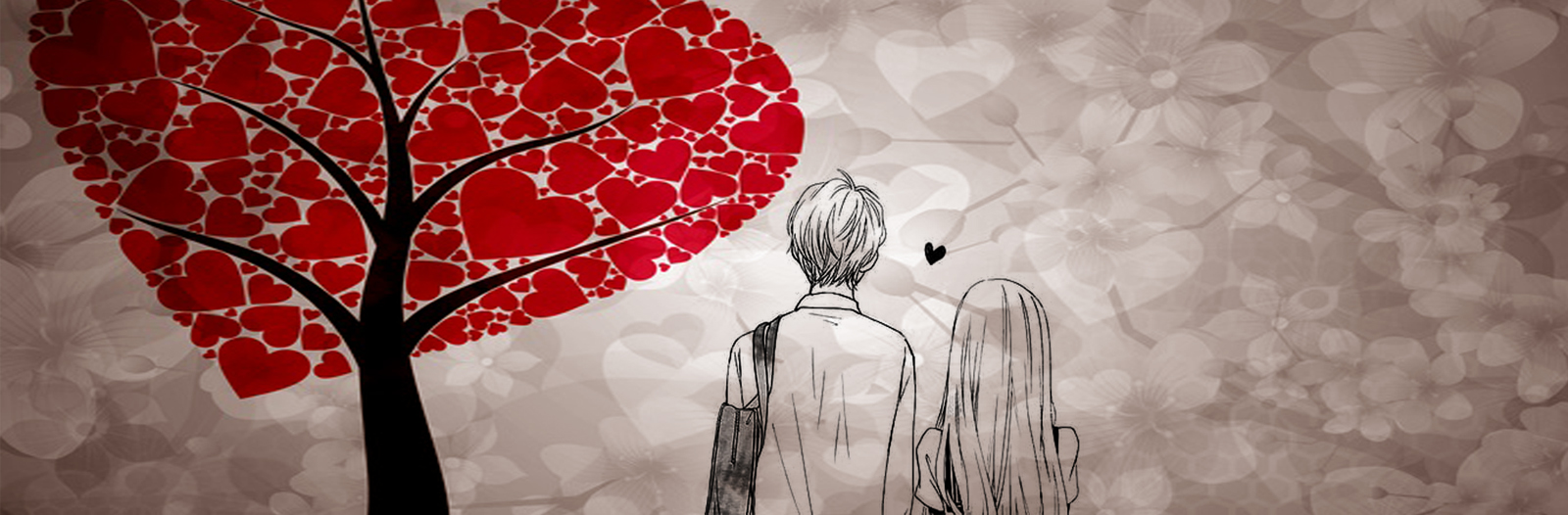১.
জুম্মনের লোল আর লহু ঠোঁটের কোণে এখনও পেঁয়াজের খোসার মত একটু খানি লেগে আছে। এটা মোটেই পানের পিকের দাগ নয়। শাহবাগ পুলিশ বক্সে এসে সে সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই দমাদম কয়েক ঘা লাগিয়ে দিয়েছে এসআই রফিক। আর গালি তো হরেক রকমের; এর মধ্যে একটি ছিল: ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে চাস, মাদারচোদ।
এরকম চাপড়-চাটি শুধু জুম্মনই না, আরোও কয়েক গণ্ডা চোর-ছেচ্চড় প্রায় প্রতিদিনই খায়। পুলিশ মহলে এসব ব্যাপার ম্যাড়মেড়ে ডালভাত। একজন পুলিশ-সদস্যের এহেন আচরণে আশেপাশের বাকি সদস্যরা বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। রফিকের একটি কল আসায় ফোন হাতে নিয়ে জুম্মনকে বলে, ‘বটগাছের নিচে গিয়ে দাঁড়া।’ জুম্মন সাথে সাথে বেরিয়ে যায়; রফিক ফোনে কথা শেষ করে পুলিশ বক্স থেকে বেরিয়ে ফুলের দোকানের পাশের বটগাছের উদ্দেশে যাত্রা করে।
একুশের বইমেলা গতকাল শেষ হলেও শাহবাগ অবধি রাস্তা এখনও যাচ্ছেতাই। ব্যানার, হোর্ডিং, পোষ্টার, বাঁশ, কাঠ এবং নানা আবর্জনায় এখনও জঞ্জালময়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ট্রাফিক সিস্টেম ঠিক হতে আরোও দুয়েকদিন লাগবে। এই প্রায়-দুপুরে এসআই রফিক জাদুঘরের উল্টোদিকের ফুলের দোকানের পাশে এসে দেখে জুম্মন ফেরিওলার কাছ থেকে কিনে ফুটপাতে বসে এক কাপ আদা-চা খাচ্ছে। রফিককে দেখে জুম্মন দাঁড়িয়ে যায়; চা-ওলাকে বলে, ‘সাররে কাপ ভাল কইরা ধুইয়া চা দে।’
রফিক কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না; খুব স্বাভাবিকভাবে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে হুস-হুস শব্দ করে চুমুক দেয়। তাদের এই পাশাপাশি অবস্থান দেখে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ঠাহর করতে পারবে না যে মাত্র আধা ঘণ্টা আগে এই পুলিশের লোকটি তার সাথে চা পানরত লোকটিকে কোনো অজ্ঞাত অপরাধে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছিল। রফিক চা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি; কাপ রাখতে রাখতেই প্রথম বলল, ‘কিচ্ছু লুকাবি না; জানে মাইরা ফেলব।’
জুম্মন অতি সহজভাবে পকেট থকে বিশ টাকার নোট বের করে চা-ওলাকে দেয় এবং তারপর বাবা জর্দা ও খয়েরসমেত একটি পান কিনে মুখে দেয়। সে আজ্ঞাসূচক কোনো মন্তব্য না করলেও রফিককে তেমন উত্তেজিত দেখাচ্ছে না। সদ্য মুখে পোরা পান আচ্ছামত দাঁতে পিষে ফুচুত করে পিক ফেলার পরই জুম্মন বলল, ‘সার, চলেন সুরার্দি উদ্যানে যাই।’ রফিক ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে বলল, ‘তুই যা, গেটের পাশেই থাকিস। আমি আসতেছি।’
জুম্মন এখন আর কোনো দলের সাথে কাজ করে না। শরীরের চামড়া-গোস্ত শিক কাবাব বানিয়ে অনেক চুরি-চামারি করেছে; কিন্তু নিজের পকেটে তেমন কিছুই আসেনি। উস্তাদই পায়ের ওপর পা তুলে বসে টাকা গুনেছে। তবে সুবিধা ছিল এই যে পুলিশি ঝামেলা, গণপিটুনির পরের চিকিৎসা ইত্যাদি উস্তাদই সামাল দিত। এভাবেই আরোও অনেকের মত জুম্মনও যখন পুলিশের চেনামুখ হয়ে গেল তখনই তার বোধোদয় হল উস্তাদের দলে থাকা আর না থাকাতো একই কথা। পুলিশের কাছাকাছি থাকতে পারলেই হল; ঝুটঝামেলা নিজে নিজেই মিটমাট করা সহজ। এর পর থেকে সে কালু, মন্টু আর মইত্যাকে নিয়ে পলাশীর সরকারি কলোনির এক রুম সাবলেট নিয়ে থাকতে আরম্ভ করে। রুমমেট তিনজনেরও একই পেশা। ওরা স্বাধীন হলেও ক্ষেত্রবিশেষে কিংবা প্রয়োজনে একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়। এসআই রফিক না বললেও জুম্মন জানে, বেঈমান কালু আঙুল দিয়ে তাকে এই বিপদে ফেলেছে। কালু বলেছিল, ‘দোস্ত, বিছানায় শুইয়াই পুরা সময় কাটাইয়া দিলাম; তোরে তো আল্লায় ছাপ্পর ফাইরা দিছে; দে না, এক হাজার টেকাই দে।’ জুম্মন কালুকে টাকা দেয়নি। বলেছে, ‘লুভ করিস না, পাবলিকে পিটাইয়া কাইলকা যুদি তোর মতো আমারও হাড্ডিগুড্ডি ভাইঙ্গা দেয়, তহন? তহন আমারে কে দিব?’
২.
ওপি-১ লটারি পেয়ে আবু নওশাদের বাবা সরকারি ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার ফরহাদ সাহেব পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি আর দেশে থাকবেন না; সপরিবারে আমেরিকা চলে যাবেন। নওশাদ তখন ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে; তার ছোটবোন শাহানা এসএসসি’র টেস্ট দিয়ে ফেলেছে এবং রেহানা দশম শ্রেণিতে উঠেছে মাত্র। ফরহাদ সাহেব বললেন, ‘প্রসেস কমপ্লিট হতে কয়েক মাস লাগবে, তোমরা নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দিতে পারবে। তারপর ওখানে গিয়ে দেখা যাবে কী হয়।’
আমেরিকায় যাওয়ার লটারি জেতা মহা ভাগ্যের ব্যাপার। ভাগ্যবান যে ক’জন লটারি জিতেছে তারাই জানে আনন্দ-উত্তেজনার পারদ কত উঁচুতে। ব্যাপারটি বাংলাদেশে নতুন বলে হুড়োহুড়ি, ছোটাছুটি বেহদ। ফরহাদ সাহেব আমেরিকান দূতাবাসে দৌড়ঝাঁপ করে লটারির ফলাফলের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এক সপ্তাহ পর ঘোষণা দিলেন তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেবেন। সরকারি চাকরি; ফাইল চলবে শম্বুক গতিতে। তাই তিনি আগেভাগেই কর্তৃপক্ষকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে চান। কিন্তু এত উচ্ছ্বাসের মধ্যেও মিসেস ফরহাদের মনটা ভারি। এত কষ্ট-কৃচ্ছ্রে গড়ে তোলা মনিপুরি পাড়ার দ্বিতল বাড়িটা ফেলে সাত-সমুদ্র তের-নদীর ওপারে গিয়ে উদ্বাস্তু হবেন। এটা ভাবতে গেলেই তার কান্না আসে। সাধের ছাদ-বাগানটার মায়া তিনি ভুলবেন কী করে! স্বামীকে তাই বলেই ফেললেন, ‘তুমি আগে চলে যাও; সবকিছু যুতসই হলে আমরা পরে আসব।’
ফরহাদ সাহেব ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ; সহজে রাগেন না। কিন্তু স্ত্রীর শিশুসুলভ কথা শুনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটু উঁচুস্বরে বললেন, ‘আমেরিকা শ্বশুরবাড়ি নাকি যে যখন ইচ্ছে তখন গিয়ে হাজির হওয়া যাবে? কপালগুণে একটা সুযোগ পাওয়া গেল, আর উনি বলছেন…।’
‘আমি তো খারাপ কিছু বলিনি। বিদেশ বিভূঁই; নতুন জায়গায় দল বেঁধে গিয়ে কোন বিপদেই না পড়ি। তার চেয়ে তুমি বরং আগেভাগে গিয়ে গোছগাছ করলে ভাল হয় না?’
ফরহাদ সাহেব উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলে ফেলায় নিজেই লজ্জিত হন। এবার গলার স্বর নামিয়ে স্ত্রীকে বলেন, ‘আরে বোকা, এখানে বয়সের একটা ব্যাপার আছে। দ্বিতীয়বার এসব ঝামেলা করতে গিয়ে কোনো কারণে দেরি হলে তোমার ছেলের বয়স পেরিয়ে যেতে পারে। তারচেয়ে বরং এক বারেই সব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলাই ভাল।’
স্ত্রীর গাঁইগুঁই থাকা সত্ত্বেও ফরহাদ সাহেব নিজের গতিতে সব কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। শাহানা-রেহানা পড়াশোনার চিন্তা বাদ দিয়ে আমেরিকার স্বপ্নে বিভোর; চোখ বুজলেই তারা স্ট্যাচু অব লিবার্টি, হোয়াইট হাউস, নায়াগ্রা ফলস, হলিউড, আরোও কত কী দেখতে পায়। তার পরও হঠাৎ করে সহপাঠী, বন্ধুদের জন্য তাদের মন খারাপ হয়ে যায়। বিশেষ করে তাদের দীর্ঘদিনের পুরনো ভাড়াটের মেয়ে রত্নার জন্য শাহানার চোখ বারবার অশ্রু সজল হয়ে পড়ে। তারা দু’জন সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
নওশাদের আমেরিকা-প্রবাসী হওয়ার ব্যাপারে তেমন কোনো উত্তেজনা নেই। তবে পরীক্ষাটা বেশি ভাল হয়নি বলে একটু মন খারাপ। প্রথমে ভেবেছিল রিজাল্ট ভাল হলে মেডিকেলে ট্রাই করবে। এখন ওপি-১ ঝামেলায় পড়ে সব গুবলেট হয়ে গিয়েছে। ভাবে, রিজাল্ট ভাল হলেইবা কী হত? আমেরিকায় ওসবের কোনো দাম নেই। ওখানে গিয়ে বুঝতে হবে কোন পথে তাকে এগুতে হবে। কিন্তু এসব সার্বিক ঝামেলার বাইরেও বুকের ভেতর একটা চিনচিনে ব্যথার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি টের পাচ্ছে নওশাদ।
নিজের পড়াশোনার বাইরে বোনদের লেখাপড়া বুঝিয়ে দেয়ার একটা অলিখিত বাড়তি দায়িত্ব পালন করে আসতে হয়েছে নওশাদকে। বান্ধবী হওয়ার সুবাদে শাহানার সাথে দোতালার ভাড়াটে রত্নাও সে সুযোগটা নিয়েছে। জটিল অংক এবং ইংরেজি বিষয়ে শাহানার পাশে বসে রত্নাও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে নওশাদের। এতে শাহানা-রেহানার মত রত্নার সাথেও নওশাদের একটা ঘরোয়া সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। অনেকদিন পর্যন্ত কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপস্থিতি না থাকলেও কলেজে যাবার পরই কেবল নওশাদ বুকের ভেতরে একটা মোচড় অনুভব করে। সেদিনের পিচ্চি রত্না এখন তার অনুভবের আলপথ ধরে কেমন ঘনঘন লাফিয়ে বেড়ায়। শাহানার সাথে পড়তে বসলেও রত্নাকে সে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি সাবলীলভাবে বোঝাতে পারে না; তার বুকটা কেমন চিনচিন করে। এতে রত্নাও একটু একটু হোঁচট খেতে থাকে। এই মিতস্ক্রিয়া এতই চাপা থাকে যে এসএসসি পরীক্ষার পর রত্না মুখ না খুললে শাহানা বুঝতেই পারত না।
মাস ছয়েকের মধ্যে ফরহাদ সাহেব আমেরিকায় যাবার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেন। গ্রাম থেকে বড় ভাইকে ডেকে নিয়ে এসে বাসার সব আসবাবপত্র বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। নীচতলার জন্য একজন ভাড়াটেও ঠিক করে ফেলেন ত্বরিত গতিতে। আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয় দোতলার কাশেম সাহেব অর্থাৎ রত্নার বাবা নিজেরটাসহ নীচতলার ভাড়ার টাকা ফরহাদ সাহেবের প্রদত্ত ব্যাংক হিসেবে জমা করবেন। তাছাড়াও বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, ট্যাক্সসহ বিভিন্ন পরিষেবার দেনা পরিশোধ ইত্যাদি বাড়তি কাজগুলোও অনেক অনুরোধ করে কাশেম সাহেবের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। পারিতোষিক হিসেবে ফরহাদ-গিন্নি বাগানসহ পুরো ছাদের একচ্ছত্র আধিপত্য কাশেম-গিন্নিকে দিয়ে দেন। এতে বেশি খুশি হয় রত্না। তার এখন ফুল-পাখি ভাল লাগার সময়। ইতিমধ্যে সে হলিক্রস কলেজের গর্বিত ছাত্রী। এসএসসির ফল ভাল হওয়াতে তারও ইচ্ছা আছে ডাক্তারি পড়ার।
আমেরিকায় গিয়ে থিতু হতে ফরহাদ সাহেবের হিসাব-নিকাশের চেয়েও বেশি ধকল পোহাতে হল। প্রথম বছর বেশ কষ্টেই কাটাতে হয়েছে বলা যায়। কিন্তু অবশেষে বাধ্য হয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসগঠন বদলিয়ে তাকে চাকরি নিতে হয় একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে; ঘটনার নাটকীয়তায় ইতিমধ্যে মুষড়ে পড়া নওশাদ কাজ পায় একটি গ্যাস ষ্টেশনে; ফরহাদ গিন্নি ল্যাংগুয়েজ শর্টকোর্স করে চাকরি পান স্কুলবাসের বাচ্চাদের ওঠানো-নামানোর। তবে শাহানা-রেহানা খুব সহজেই স্কুলে ভর্তি হয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। ফরহাদ সাহেবের ইচ্ছা, মেয়েরা খুব ভাল করে পড়ুক এবং উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করুক। এভাবে মার্কিন জীবনধারায় নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে করতেই চারটি বছর বিদ্যুৎগতিতে চলে যায়। এর মধ্যে তাদের কারুরই দেশে আসা হয়নি। এই ফাঁকে এখানে অনেক অঘটনও ঘটে যায়।
এক বছর পেরোতে না পেরোতেই বড় ভাই আরশাদ ছোট ভাই ফরহাদকে চিঠি লেখেন তার মনিপুরের বাড়িটি যেন তাকে দিয়ে দেন। কারণ হিসেবে তিনি তিন পাতাভর্তি বিস্তারিত যুক্তিও তুলে ধরেন। যেমন, ছোট ভাইকে মানুষ করতে বাপের সাথে সাথে তারও অনেক অবদান আছে। তাই দেশে থাকাকালেও ফরহাদ একটা উন্নত জীবন যাপন করতে পেরেছেন। আর এখন আমেরিকায় যাওয়ার পর এই বাড়ি তার কাছে এক তুচ্ছ জিনিশ। বড় ভাই হিসেবে বিত্তবান ছোট ভাইয়ের কাছে তিনি এ দাবি করতেই পারেন।
দূর প্রবাস থেকে ফরহাদ সাহেব যতটুকু সম্ভব পারিবারিকভাবে এ বিষয় নিয়ে দেন দরবার করেছেন। তা করতে গিয়ে খাড়ার ঘা হিসেবে তার দুই বোনও হাজির হয়েছে। তাদের কথা হল, বড় ভাই একা সে বাড়ি পেতে পারেন না; সেখানে তাদেরও হক আছে। ধুন্ধুমারের শেষ পর্যায়ে ফরহাদ সাহেব অগত্যা বড় ভাইয়ের অনুকূলে একটা সমাধান খুঁজে বের করেন। তিনি বলেন যে বাড়িতে এসে তিনি যা করার করবেন, তবে আপাতত বাড়িভাড়াটা যেন বড় ভাই নিয়ে নেন।
বাড়ি নিয়ে সাময়িক সুরাহা হলেও ফরহাদ সাহেব ভাইবোনদের আচরণে মনে খুব কষ্ট পান। ভাইবোনদের প্রতি তার অনেক দরদ ছিল; তাদের জন্য কিছু করারও প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অল্পদিনেই তারা এমন অচেনা মানুষ হয়ে যাবে এটা ভাবতেও পারেননি। তাই যতই সময় গড়িয়েছে দেশের প্রতি তার অনীহা ও অবিশ্বাস ক্রমশ বেড়েছে। আত্মীয়স্বজনের সাথে এক সময় তাই সম্পর্ক ছেদ করে ফেলেন তিনি। ফলস্বরুপ, তৃতীয় বছরের শেষ দিকে জুতসই একজন খদ্দের পেয়ে আমেরিকায় বসেই তিনি তার বহু কষ্টের ফসল মনিপুরি পাড়ার বাড়িটি বিক্রি করে দেন। এর অনেক বছর পর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বাবা-মার কবর জিয়ারতের জন্য একবারই দেশে এসেছেন। ততদিনে অবশ্য বড়ভাইও গত হয়েছেন।
ওদিকে আমেরিকার জীবন থেমে থাকেনি। সময়ের স্রোতে জীবন তার স্বাভাবিক নিয়মে এগিয়ে চলেছে নির্মোঘ গন্তব্যের দিকে। ফরহাদ দম্পতি বার্ধক্যে পৌঁছেছেন। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে সে অনেক দিন – তারা তাদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। তবে জীবনের পথ যেমন সরলরৈখিক নয় ফরহাদ সাহেবের সংসারের সুখও তেমন নিরবচ্ছিন্ন হয়নি। নওশাদের বয়স পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেলেও সে এখনও বিয়ে করেনি, করতে চায়ও না। সে এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী; জ্যাকসন হাইটস-এ ওরিয়েন্টাল ফুডস-এর ব্যবসা রমরমা। বাবা-মা’রা না এলেও সে বেশ ক’বার বাংলাদেশ ঘুরে গেছে, তবে পরিবারের কারুর সাথে দেখা করেনি। বাংলাদেশে আসার সময় প্রতিবারই মা পই পই করে বলেছেন, দেশ থেকে যেন তার পছন্দমত একটা মেয়ের সন্ধান নিয়ে আসে; তারা দেশে গিয়ে ঘটা করে ছেলের বিয়ে দেবেন। কিন্তু না, তেমনটি ঘটেনি।
৩.
এসআই রফিকের কাছে কিছু লুকিয়ে পার পাবে না জুম্মন; তাই যা ঘটেছিল তা গড়গড় করে বলে দিয়েছে।
রফিক জিজ্ঞেস করে, ‘তাইলে তুই জানতে পারস নাই লোকটাকে কোন হসপিটালে নেয়া হয়েছে?’
‘আমিতো আর দাঁড়াই নাই, সার। দিনটা ছিল শুক্কুরবার; তা-ও বইমেলা শেষ হওয়ার তিনদিন আগে, শেরাটনের সামনে দিয়া লোকটা রাস্তা পারাইতেছিল। তহনই এক পাগলাচোদা বাস তারে ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া ভাগছে। হেরপর আরোও কয়েকজনের লগে আমিও চিল্লাপাল্লা কইরা লোকটারে উঠাইতে গেছি। যাইয়াই আমি তার বেগটা লইয়াই কান্ধে ঝুলাইছি। লোকজনের ভিড় যহন বাড়ছে, তহনি আমি কাইটা পড়ছি। এর পরে লোকটার কী অইছে কইতে পারুম না।’
‘আচ্ছা যাউক।’ রফিক বলে, ‘তারপর তুই একলাই ব্যাকপ্যাকটা হজম কইরা ফেললি?’
জুম্মন জিহ্বায় কামড় দিয়ে বলে, ‘এ কী সম্ভব সার। আমি ভাবছি মেলার শেষ দুই তিনটা দিন একটু ধাক্কাধাক্কি কইরা কিছু কামাইয়া লই, এর পরেতো আপনার কাছে আইতেই অইবো।’
রফিক বলে, ‘বুঝছি, সন্ধ্যার পরে ব্যাকপ্যাক নিয়া আসবি, আর কোনো চালাকি না কইরা ইমানদারিতে ঠিক ঠিক বিবরণ দিবি। তারপর তোরে নিয়া পিজিতে একটা ঢুঁ মারব…’
‘কিন্তু সার…!’ হাসপাতালের কথা শুনে জুম্মন আঁতকে ওঠে। লোকটা যদি পিজিতে চিকিৎসাধীন থাকে তাহলে আম-ছালা দুইই যাবে।
‘চিন্তা করিস না, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসছে। বিদেশি লোকতো!’ বলে জুম্মনের দিকে তাকিয়ে রফিক চোখ মারে।
মাগরেবের পরপর জুম্মন ব্যাকপ্যাক নিয়ে ফিরে এলে রফিক বলে, ‘শুধু পাসপোর্টটা বাইর কর।’
জুম্মন কভারে মোড়া একটি বিদেশী পাসপোর্ট বের করার সাথে সাথে রফিক ব্যাকপ্যাকটা টান দিয়ে নিয়ে তার ড্রয়ারে তালাবদ্ধ করে রাখে। তারপর জুম্মনকে চোখের ইশারায় বের হতে বলে সে-ও বেরিয়ে পড়ে।
বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে চা-সিঙ্গাড়া খেতে খেতে রফিক জুম্মনের কাছে ব্যাকপ্যাকের মালামালের বিবরণ চায়। জুম্মন মুখস্থ বলে যায়, ‘একটা ফুলহাতা সোয়েটার, একটা ছোট সেন্টের শিশি, পাঁচটা একশ’ ডলারের নোট, সাড়ে চার হাজার বাংলা টাকা, পাসপোর্ট, কয়েকটা প্লাস্টিকের কার্ড আর কিছু কাগজপত্র।’
রফিক চোখ চিকন করে জিজ্ঞেস করে, ‘ব্যাগে সবকিছু ঠিকঠাক মত আছে তো?’
জুম্মন মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ‘হ, সব ঠিক আছে; তয় টেকাটা আমি বিকাশ কইরা বাড়িতে পাঠাইয়া দিছি সার।’
রফিক চোখ লাল করে ‘হারামজাদা’ বলে সবেগে হাতটা উঠিয়েছিল, কিন্তু জুম্মনের গালে না বসিয়ে কী ভেবে তা নামিয়ে ফেলে। তারপর বলে, ‘চল।’
জুম্মন বলে, ‘দাড়ান সার, একটা পান মুখে দিয়া নেই।’
রুগিদের কিংবা মৃতদের তালিকা কোন টেবিলে কার কাছে পাওয়া যাবে এসব রফিকের কেন পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলেরই জানা আছে। সে সংশ্লিষ্টদের কাছে দুর্ঘটনায় ভর্তি হওয়া রুগীদের ব্যাপারে বিশদভাবে জানতে চাইল। তারা বলল, এটাতো জানা কথা, দুর্ঘটনায় আহত চার-পাঁচজন দৈনিকই আসে। তবে গত এক সপ্তাহে যারা এসেছিল তাদের কাউকে ভর্তি হতে হয়নি। অবশ্য গুরুতর আহত একজনকে হাসপাতালে আনার পথেই মারা গেছে।
রফিক ও জুম্মন একথা শুনে কেঁপে ওঠে। রফিক বলে, ‘আচ্ছা, আপনাদের রেকর্ড চেক করে দেখেন তো এই লোকটার নাম কোথাও আছে নাকি।’ একথা বলে সে পাসপোর্টের নামটি দেখায়।
তখন হাসপাতালের একজন লোক বিভিন্ন রেজিস্টার চেক করে মাথা নাড়িয়ে বলল, ‘না, নেই।’ তবে আরেকটা কথা, ওই মৃত লোকটাকে কোন চিকিৎসাই দিতে হয়নি। স্ট্রেচারের উপরেই দুই তিনজন ডাক্তার একটু চেক করে ডেড ডিক্লেয়ার করে চলে গেছেন।’
রফিক অস্থিরভাবে বলে, ‘তারপর আত্মীয়স্বজনরা লাশ নিয়ে গেছেন? আচ্ছা লোকটার বাসার ঠিকানা জানেন, বাই চান্স?’
হাসপাতালের অন্য একজন অধস্তন কর্মচারী বলল, ‘ঠিকানা পাইব কই সার; কয়েকজন লোক ধরাধরি কইরা রাস্তাত্থন উঠাইয়া আইনা থুইয়া গেছেগা।’
রফিক তখন পাসপোর্টটি খুলে ধরে সবাইকে দেখিয়ে বলে, ‘দেখেনতো, লোকটি কী দেখতে এ রকম?’
উপস্থিত সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাসপোর্টের ছবি দেখে একেক রকম মন্তব্য করার সময় হঠাৎ একজন চিৎকার করে তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া নিউরোসার্জন মোহসেনা হাসানকে দেখিয়ে বলে, ‘এই যে এই ম্যাডামও সেদিন ছিলেন।’
রফিক দ্রুত চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে মহিলা ডাক্তারের পথ আগলে বলে, ‘এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করেন।’
ডাক্তার ম্যাডাম জিজ্ঞাসু নেত্রে সবার মুখের দিকে তাকালে রফিক পাসপোর্টটি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, ‘এই লোকটি চারদিন আগে শেরাটনের সামনে রোড অ্যাকসিডেন্ট করেছে; পাসপোর্টটি দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গেছে।’
ডাক্তার ম্যাডাম এক পলক পাসপোর্টের ছবিতে চোখ বুলিয়ে বললেন, ‘এভাবে তো বলতে পারব না। এই লোকই মারা যাওয়া লোক ছিল কিনা জানিনা। মাথায় সিরিয়াস ইনজুরি ছিল। এ অবস্থায় লোকজনের চেহারা ঠিক থাকে না।’ তারপর হাসপাতালের স্টাফদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আচ্ছা, ওই লোকটাকে আঞ্জুমানে হ্যাণ্ডওভার করা হয়েছে না?’
অধস্তন কর্মচারীটি বলল, ‘হ ম্যাডাম, গতকাইল।’ সে আরেকটু যোগ করে বলল, ‘এই লোকই হইতে পারে ম্যাডাম; আমরাতো টানাটানি করছি।’
ডাক্তার ম্যাডাম ‘ভেরি স্যাড’ বলে পাসপোর্টের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকালেন। এরপর তার চোখের কাছাকাছি নিয়ে এসে নাম ঠিকানাসহ পাসপোর্টের অন্যান্য তথ্যাদি পড়ে মনে হল তিনি হঠাৎ স্থির হয়ে গেলেন। ‘এটা ইউএস পাসপোর্ট বলে মনে হচ্ছে’ বলে পাসপোর্টের মলাটের রং দেখার জন্য চামড়ার কভারটি খুলতে চেষ্টা করলেন। তখনই কভারের ভেতর থেকে টুপ করে একটি অল্পবয়সী মেয়ের ছবি মেঝের উপর পড়ে যায়। ডাক্তার ম্যাডাম নিজেই ফ্লোর থেকে দ্রুত ছবিটি উঠিয়ে তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। ছবি দেখে তিনি অনুভব করেন তার শরীরের রক্তপ্রবাহ বেড়ে গেছে; কিন্তু সাবধানতার সাথে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন।
এসআই রফিক তখন মুখ খোলে, ‘কোনো ক্লু পেলেন ম্যাডাম?’
ডাক্তার ম্যাডামের ধারনা, তিনি একটা ক্লুর কাছাকাছি যেতে পেরেছেন। কিন্তু একথা না বলে তিনি এসআই রফিককে বললেন, ‘আপনি কি পাসপোর্ট আর এই ছবিটা আমার কাছে রেখে যেতে পারবেন? এমনও হতে পারে এই লোকটার খোঁজে তার কোনো আত্মীয়স্বজন আসতে পারে।’
রফিক জুম্মনের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে, রেখে দেন। আমি দু’চার দিন পর একবার খোঁজ নেব।’
৪.
হার্ট-স্পেশালিষ্ট প্রফেসর আবিদুল হাসানের ফিরতে দেরি হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের যেমনটি হয়, সরকারি চাকরির পাশাপাশি তিনিও দু’তিনটি প্রাইভেট হসপিটালের সাথে জড়িত; আজ দু’টি অপারেশন আছে। সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত নিউরোসার্জন মোহসেনা আবিদ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসাবে স্বামীর সাথেই পিজিতে কর্মরত। তিনিও প্রাইভেটের সাথে জড়িত। আজকে তার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকায় সোজা বাসায় এসে শাওয়ার নিয়ে ছেলে মেয়ের সাথে ডিনার সেরে ফেলেছেন। অবশ্য আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলেও তিনি তা বাতিল করে দিতেন; কারণ তিনি আজ মানসিকভাবে বিধ্বস্ত।
মেয়ে তৃণা সলিমুল্লাহ মেডিকেলে চান্স পেয়ে পূর্ণোদ্যমে বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে থাকে। ছেলে অর্ক নটরডেম কলেজে পড়ছে; তার ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা নেই। আইটিতে তার আগ্রহ বেশি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই তারা তাদের রুমে ফিরে গেলেও গৃহকর্ত্রী ডাক্তার মোহসেনা একটু ধীরে ধীরে খেতে খেতে গৃহপরিচারিকাদের সাথে সাংসারিক কথাবার্তা সেরে নেন। প্রতিদিন তিনি ডিনার সেরে কিছুক্ষণ টেলিভিশনের রিমোট নাড়াচাড়া করেন। কিন্তু আজ তিনি ড্রইং রুমে না বসে সরাসরি শোবার ঘরে চলে যান। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। পার্স খুলে দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া ব্যক্তির পাসপোর্টটি খুলতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করছেন। তিনি বুঝতে পারছেন না এখন তিনি কী করবেন। পাসপোর্টের ছবির লোকটির চেহারা এত বছরে অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে; গালে চর্বি-মাংস জমেছে, কপাল প্রশস্ত হয়েছে, চুলের ছাট ছোট বলে কতটুকু পাতলা হয়েছে তা ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে না। তাই নামটি খুঁটিয়ে না পড়লে তার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠত না মোটেই। আবু নওশাদ নামটি আমেরিকান পাসপোর্টে ছাপা দেখেই তার ধূলিধূসর স্মৃতির আয়না পরিষ্কার হয়ে যায়।
মনিপুরি পাড়ার বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেলে রত্নারা বাধ্য হয়ে কাঠালবাগানে একটা ভাড়া বাসায় গিয়ে ওঠে। সে অবধি শাহানার পত্রালাপ ছিল রত্নার সাথে। তখন টেলিফোন সহজলভ্য ছিল না, আর মোবাইল ফোনতো আসেইনি। তাই চিঠিই মূলত যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ছিল। বাড়ি নিয়ে ফরহাদ সাহেবের পরিবারে জটিলতা শুরু হয়ে গেলে নির্ঝঞ্ঝাট কাশেম সাহেব বেশ অস্বস্তি বোধ করেন এবং ফরহাদ সাহেবের পরিবারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। রত্না ততদিনে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে; অতএব তার নির্বিঘ্ন পড়াশোনার জন্য একটি শান্ত পরিবেশেরও প্রয়োজন। ঠিক এরকম সময়ে ফরহাদ সাহেব বাড়িটি বিক্রি করে দিলে কাশেম সাহেব হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।
শাহানার চিঠিতে প্রথম প্রথম হালকা খুনসুটি থাকত, কিন্তু রত্না এসব সজ্ঞানে এড়িয়ে যেত। কারণ অনেকটা এরকম যে সোজা-সরল নওশাদের সাথে তার কোনো রসায়ন তৈরির সুযোগই হয়নি। তাছাড়া সময়ের সাথে সাথে সে পরিপক্ব হয়ে উঠলে এবং তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগুতে থাকলে বাস্তবতা সম্বন্ধে সে অধিক সাবধানী হয়ে ওঠে। রত্না ভালভাবে বুঝতে পারে নওশাদ একদিন হয়ত অনেক টাকার মালিক হবে, কিন্তু নিজের পাশে জীবনসঙ্গী হিসেবে তাকে ভাবা যাবে না। হয়তোবা সে তার ক্ষীণ মনোবৈকল্যকে আশকারা না দেবার জন্যই কাঠালবাগানে যাবার পর লেখাপড়ায় অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং শাহানার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে।
এর পরের ঘটনাবলীতে তেমন নাটকীয়তা না থাকলেও কিছু আকস্মিকতা ছিল। রত্না মেডিকেলের দ্বিতীয় বর্ষে পা দিতেই এক শরিফ পরিবারের সদ্য পাশ করা সুদর্শন এক ডাক্তার-ছেলের কাছ থেকে কাশেম সাহেবের কাছে জোর প্রস্তাব আসে। ছেলেটিকে যে রত্না চিনে না এমন নয়। বেশ ক’বার তার সাথে ছেলেটি কথা বলেছে। রত্নাও তাকে যথেষ্ট সমীহ করেছে। ছেলেটির অনেক ইঙ্গিতপূর্ণ কথাকে রত্না কৌশলে এড়িয়ে গেছে এজন্য যে পড়াশোনার এই স্তরে তার অধ্যবসায়ে বিঘ্ন ঘটুক এমন কিছুতে সে জড়াবে না। কিন্তু নিয়তিকে সে এড়িয়ে যাবে কেমন করে? ছেলেটির বাবা যখন কাশেম সাহেবকে বললেন, ‘দেখুন ভাই, আমি একজন প্রকৌশলী; আমি যখন বিয়ে করেছি তখন আমার স্ত্রী মেডিকেলে ভর্তি হয়েছে মাত্র। আল্লাহ্র রহমতে সে ভালভাবেই লেখাপড়া শেষ করেছে, কোনো অসুবিধা হয়নি। আপনার মেয়েকে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। তার লেখাপড়ার দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দেন।’
অগত্যা কাশেম দম্পতি মেয়েকে রাজি করান। তাছাড়া রত্না যতটুকু দেখেছে তাতে ছেলেটি মোটেই ফেলনা নয়; বরং বলা চলে অনেক মেয়েরই হৃদয়ের স্পন্দন। অতএব অল্প কিছুদিনের মধ্যে শুভকর্মটি সম্পন্ন হয়ে যায়। আরোও কিছুদিন পর ডাক্তার স্বামী আবিদ হাসান বিসিএস দিয়ে কর্মজীবনে ঢুকে পড়ে আর ওদিকে অনুকূল পরিবেশে রত্না কৃতিত্বের সাথে পাঠ চুকিয়ে ডাক্তার মোহসেনা হাসান হয়ে ওঠে। অনিবার্যভাবে সে-ও বিসিএসের মাধ্যমে তার ক্যারিয়ার শুরু করে। তাছাড়া, আধুনিক পরিবারে সচরাচর এমনটি না ঘটলেও সবাইকে চমকে দিয়ে ছাত্রাবস্থায়ই রত্না দুই সন্তানের মা হয়ে যায়।
নিউরোসার্জন মোহসেনা হাসান তার পার্স থেকে পাসপোর্টটি হাতে নিয়ে দু’চোখ বন্ধ করে দোলচেয়ারে বসে অতীতের বিচ্ছিন্ন অলিগলি ঘুরে আসেন। তিনি নিশ্চিত এই পাসপোর্টের নওশাদই সেই নওশাদ। পাসপোর্টের কভারে পাওয়া ছোট্ট মেয়ের ছবিটি তার নিজেরই। আমেরিকা চলে যাবার আগে লজ্জা ভেঙ্গে নওশাদ ভাই তার একটি ছবি চেয়েছিলেন। সেই বোকা-বয়সের রত্না লুকিয়ে ছাদে গিয়ে নওশাদ ভাইকে ছবিটি দিয়েছিল। নওশাদ ভাই তখন মায়ের ছাদ-বাগান থেকে একটি গোলাপ ছিঁড়ে কাঁপাহাতে তাকে তুলে দিয়ে বলেছিল, ‘রত্না, কোনোদিন বলতে পারিনি, আর কখনও বলার সুযোগও পাব না; আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।’ সেই মূহুর্তটিই ছিল রত্নার জীবনের প্রথম শিহরণ। নওশাদ ভাইয়ের কথা শেষ না হতেই ভোঁ দৌড়ে সে পালিয়ে বেঁচেছিল।
ডাক্তার মোহসেনা এবার চোখ খুলে তার পুরনো ছবিটি পাসপোর্টের কভারের ভেতর থেকে বের করেন। তিনি ভাল করে সেদিনের রত্নাকে দেখতে থাকেন। কোনো এক স্টুডিয়োতে তোলা ছবি। কোনো দাগ পড়েনি; এখনও ঝকঝকে। তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। হঠাৎ ছবিটির পেছন দিকে তার চোখ পড়ে। ডাক্তার মোহসেনা এবার চরম অস্থিরতা বোধ করেন। ওখানে গুটিগুটি অক্ষরে লেখা রয়েছে, ‘রত্না, আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি।’
ওই লেখার ওপর ডাক্তার মোহসেনার দু’ফোটা অশ্রু টুপ করে ঝরে পড়ে।